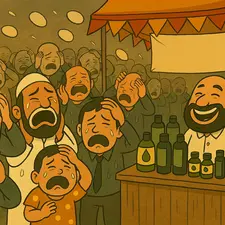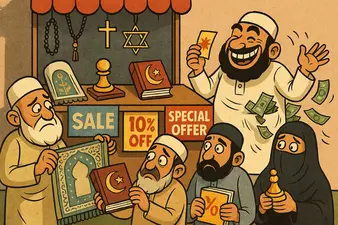তিউনিসিয়ার বিপ্লবের ছায়া
বাংলাদেশ কি ব্যর্থতার পথে হাঁটছে?

২০১১ সালের তিউনিসিয়ার ‘জেসমিন বিপ্লব’ একসময় গণতন্ত্রের প্রতীক হিসেবে উদযাপিত হয়েছিল। কিন্তু এক দশকের ব্যবধানে সেই বিপ্লব আজ ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি। দুর্বল রাষ্ট্রক্ষমতা, অলিগার্কদের দখলদারিত্ব, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের অভাবে তিউনিসিয়া ঘুরপাক খাচ্ছে হতাশার চক্রে। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের সরকার পতন পরবর্তী বাস্তবতায় এই বিপ্লবের সঙ্গে অস্বস্তিকর মিল ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
তিউনিসিয়ার মতো বাংলাদেশেও গণ-আন্দোলনের পর রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের দ্বন্দ্বে নিমগ্ন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও প্রশাসনিক সংস্কার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রশ্নে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। শিল্প খাত অনিশ্চয়তায়, কর্মসংস্থান স্থবির, সামাজিক সূচক থমকে আছে। শহুরে নিম্ন আয়ের মানুষ ও গ্রামীণ প্রান্তিক শ্রেণী জীবনযাত্রার ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্বের হার ঊর্ধ্বমুখী। গণ-অভ্যুত্থানের সময় যেসব দাবি ছিল—স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, প্রশাসনিক সংস্কার—সেগুলো ধীরে ধীরে আড়ালে চলে যাচ্ছে।
এই সংকটকে আরও গভীর করেছে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলোর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস। আইএমএফের পরামর্শে ভর্তুকি হ্রাস, সরকারি ব্যয় সংকোচন, এবং বাজারমুখী সংস্কার বাস্তবায়নের ফলে সামগ্রিক উৎপাদন ও কর্মসংস্থানে মারাত্মক সংকট তৈরি হয়েছে। তিউনিসিয়ার মতো বাংলাদেশেও দেখা যাচ্ছে—অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের নামে জনকল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগ কমছে, অথচ ঋণের বোঝা বাড়ছে। ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জনগণের প্রবেশাধিকার সংকুচিত হচ্ছে।
তিউনিসিয়ায় রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শিক বিভাজন যেমন সংবিধান বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করেছিল, বাংলাদেশেও রাজনৈতিক অনৈক্য সেই একই পথে হাঁটছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ছয় মাস পূর্তিতে প্রকাশিত বিশ্লেষণগুলোতে উঠে এসেছে—সংবিধান, মানবাধিকার, ক্ষমতার ভারসাম্য—সবই কাগজে থাকলেও বাস্তব প্রয়োগে ঘাটতি রয়েছে। তিউনিসিয়ার মতো বাংলাদেশেও পুরনো সুবিধাভোগী গোষ্ঠী নতুন রূপে ফিরে আসছে, যা গণতন্ত্রের কাঠামোকে দুর্বল করে তুলছে।
এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের সামনে করণীয় হলো—প্রথমত, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কার্যকর সংলাপ ও ঐকমত্য গড়ে তোলা। মতাদর্শিক বিভাজনকে অতিক্রম করে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রশাসনিক সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে—স্বাধীন নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সাংবিধানিক আদালতকে কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তৃতীয়ত, আইএমএফ-নির্দেশিত পুনর্বিন্যাসের পরিবর্তে স্থানীয় বাস্তবতা ও জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীও উন্নয়নের সুফল পায়।
তিউনিসিয়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, শুধু ভোটাধিকার দিয়ে গণতন্ত্র টিকে থাকে না—জরুরি হলো অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি। বাংলাদেশ যদি এই শিক্ষা গ্রহণ না করে, তাহলে পরিবর্তনের স্বপ্নও তিউনিসিয়ার মতো হতাশায় পর্যবসিত হবে।