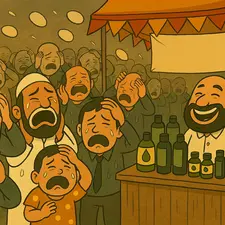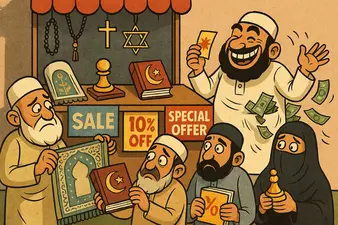মতামত
আর্মচেয়ার প্রবৃত্তির আর্মচেয়ার নেশন: ফেরার পথ নেই, থাকে না কোনোকালে?

১
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উত্থান আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন এনেছে। আগে যেখানে মতামত প্রকাশের জন্য দরকার হতো একটি সংবাদপত্রের কলাম, একটি সংগঠিত সভা, অথবা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক প্ল্যাটফর্ম, এখন একটি মোবাইল স্ক্রিন আর ইন্টারনেট সংযোগই যথেষ্ট। এর ফলে আমরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছি মতামতদাতা, বিশ্লেষক, এমনকি বিশেষজ্ঞ। এই সহজলভ্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মধ্যে তৈরি করেছে এক নতুন জাতিগত বৈশিষ্ট্য। আমরা হয়ে উঠছি এক ‘আর্মচেয়ার নেশন’। আমরা সবাই এখন কোনো না কোনো পর্যায়ের ‘আর্মচেয়ার’ একটা কিছু বনে গেছি। কেউ আর্মচেয়ার পলিটিসিয়ান, কেউ আর্মচেয়ার হিস্টরিয়ান, কেউ আর্মচেয়ার ইকোনমিস্ট। গভীরভাবে না জেনেই রাজনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি বিষয়ে রায় দিচ্ছি, সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, তর্কে নামছি। বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, মাঠপর্যায়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু “আমার জানা”, “আমার দেখা” বা “আমার সোর্স” বললেই যেন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে।
এই প্রবৃত্তি আমাদের এক গভীর বিভ্রমে ফেলছে। আমরা আর তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করছি না। যে কোনো সামাজিক ঘটনা, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, কিংবা ঐতিহাসিক আলোচনাতেই আমরা এখন গলা উঁচু করি, কিন্তু তলিয়ে দেখি না। এভাবেই আমরা ক্রমশ পরিণত হচ্ছি এক আর্মচেয়ার নেশনে। যারা জ্ঞানের গভীরে যাওয়ার চেয়ে, সত্য অনুসন্ধানের চেয়ে নিজস্ব মতামতের জগতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি ।
কিন্তু সমস্যা এখানেই। এই ‘আর্মচেয়ার প্রবৃত্তি’ আমাদের করে তুলেছে সবচেয়ে অরক্ষিত জাতিতে। কারণ, আমরা এখন সহজেই বিভ্রান্ত হই। যে কোনো গুজব শুনেই বিশ্বাস করি। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দেখেই শেয়ার করি। রিলস কিংবা ক্লিপ দেখেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাই। যে প্রক্রিয়ায় আগে মতামত গঠিত হতো, তাতে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গবেষক, সম্পাদক ইত্যাদি নানা বর্গের বিশেষজ্ঞরা যুক্ত থাকতেন। সবাই মিলে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার একটা বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর হিসেবে কাজ করতেন। সে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তর এখন প্রতিস্থাপিত হয়েছে স্মার্টফোনের স্ক্রিন স্ক্রল করা ‘আর্মচেয়ার প্রবৃত্তি’ দিয়ে। আগে প্রথাগত সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে যখন তথ্য ছড়াত, সেসময় সংবাদমাধ্যমগুলোর তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া ‘ফিল্টার’-এর কাজ করতো। কিন্তু এখনকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উন্মত্ত যুগে প্রত্যেকে নিজেরাই সংবাদমাধ্যম। ফলে তাতে কোনো ফিল্টার নেই, দায়িত্ববোধও নেই। আর এই শূন্যস্থানই তৈরি করছে বিভ্রান্তির এক মহাসাগর। যেখানে ভাসছে অর্ধসত্য, গুজব, আর বিকৃত ইতিহাস।
২
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সেই চূড়ান্ত মুহুর্ত, যখন বাঙালি প্রথমবার নিজের ভাগ্য নিজ হাতে নিতে পেরেছিল। তার সাথে সাথেই শুরু হয় আরেক লড়াই—নিজের ইতিহাস লেখার লড়াই।
তার বিপরীতে স্বাধীনতার পরপরই দেখা দেয় ইতিহাসের উল্টো রথের প্রচেষ্টা। ১৯৭২ সালে মুক্তি পায় সুভাস দত্তের ‘অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী’। পরিচালকের অভিযোগ, সে ছবির সাফল্যকে ব্যাহত করেছিল মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের ষড়যন্ত্র। সত্তরের দশকের শেষভাগেই, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেই শক্তির প্রকাশ্য প্রদর্শনী দেখা যায়। সেই সভা থেকে ডাক আসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পাল্টানোর। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান বদলে পাকিস্তানি আদলে ফিরিয়ে নেয়ার।
এই প্রচেষ্টা কখনো থামেনি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেবল কৌশল বদলেছে। সুযোগ বুঝে কখনো ইতিহাসের বইয়ে ঢুকেছে, কখনো রাজনীতির মাঠে, কখনো সংস্কৃতি চর্চার আড়ালে। কিন্তু বরাবারই তাদের রুখে দিয়ে আসছিল দেশের সাহিত্যিক গোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক-সামাজিক কর্মীরা। তাদের সঙ্গে মূলধারার অধিকাংশ সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমগুলো। তাড়া হয়ে ছিলেন সময়ের ‘ফিল্টার’ হয়ে। কিন্তু যখন প্রথাগত গণমাধ্যম থেকে ভারসাম্য সরে চলে এল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, যেখানে প্রত্যেকে নিজেই সংবাদদাতা, বিশ্লেষক, ও প্রচারক, সেই পুরোনো প্রতিরোধের কাঠামোটা ভেঙে পরল। শুরু হলো এক ‘আনফিল্টারড এরা’। যেখানে মিথ্যা খবর, গুজব, আর বিকৃত ইতিহাস শুরু করল রামরাজত্ব।
৩
এই ‘আনফিল্টারড এরা’তে আমরা পরিণত হয়েছি এক ‘আর্মচেয়ার নেশন’-এ। যেখানে প্রত্যেকেই ‘হনু-বিশেষজ্ঞ’, ‘হনু-গবেষক’। সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতা বা মতকে সার্বজনীন সত্য ধরে নিচ্ছে, আর তথ্যকে ব্যবহার করছে কেবল সেই মতের পক্ষে যুক্তি হিসেবে। ফলে তৈরি হয়েছে এক বিপজ্জনক বাস্তবতা। আমরা এখন খুব সহজেই গুজবে বিশ্বাস করি, বিকৃত ইতিহাসে নির্ভর করি, ভুল ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হই। আজকের বাংলাদেশে যত দ্রুত তথ্য আসে, তার চেয়েও দ্রুত ছড়ায় অর্ধসত্য। একজনের মন্তব্য, একটা ক্লিপ, একটা ফরোয়ার্ডেড মেসেজ—এসবই এখন আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে আমাদের ইতিহাসবোধে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সভ্যতার সর্বোচ্চ অর্জন। আমাদের আত্মপরিচয়ের মেরুদণ্ড। অথচ আজ সেই মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই নানা বিভ্রান্তি, বিকৃতি, এবং কল্পিত বয়ানের ছড়াছড়ি সবচেয়ে বেশি। কেউ মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে, কেউ শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক তুলছে, কেউ আবার ঘোমটা ফেলে ফিরে যাচ্ছে যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি প্রচারের ছাঁচে। আর এসব যে হতে পারছে, তার পটভূমি হিসেবে কাজ করছে আমাদের আর্মচেয়ার প্রবৃত্তি। আমরা ভাবি, সামাজিক মাধ্যমে কিছু পোস্ট পড়ে, কিছু ভিডিও দেখে, বা জনপ্রিয় ভ্লগ শুনলেই ইতিহাস জানা যায়। মনে করতে চাই না, ইতিহাস একটা বিশেষায়িত জ্ঞান। তার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হয়। বুঝতে চাই না, ইতিহাস বোঝা মানে শুধু তথ্য জানা নয়, বরং প্রেক্ষাপটটা বোঝা, সংগ্রামকে উপলব্ধি করা।
ফলাফল, অসংখ্য ভুল জানা মানুষের সমষ্টিতে আমরা হয়ে উঠছি এক ভুল জানা জাতি। যাদের সত্য-মিথ্যার সীমানা অস্পষ্ট। ইতিহাস আর মতামতের সীমারেখা মিলেমিশে একাকার। আর যখন কোনো জাতি তার ইতিহাস ভুলভাবে জানে, তখন তার ভবিষ্যৎও নিশ্চিতভাবেই ভুল পথে চলতে থাকে।
৪
এই আর্মচেয়ার প্রবৃত্তি থেকে কি আদৌ কোনো মুক্তির পথ আছে? আছে কি আর্মচেয়ার নেশন থেকে বেরিয়ে আসার কোনো টোটকা?
আছে তো অবশ্যই। কিন্তু সে পথে আমোদ নেই। মজমা নেই। সেই একমাত্র টোটকা আরাম কেদারায় আধশোয়া থেকে উপভোগের আনন্দ ছেড়ে বেরিয়ে আসা। তথ্য যাচাই করতে শেখা। মত গঠনের আগে যুক্তি শোনা। নিজের সীমাবদ্ধতা জানা। সবজান্তা শমশের ভাবনা ছেড়ে যার যার বিষয়ের শমশেরদের মূল্য দেয়া। আর মনে রাখা, যে জাতি তার ইতিহাসকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে রাখে, সে জাতি কখনোই সত্যিকার অর্থে মুক্ত থাকতে পারে না।
কিংবা আরো রূঢ়ভাবে বললে, যে জাতি তার ইতিহাসকে মনে রাখে না, ইতিহাসও সে জাতিকে মনে রাখে না। আর ইতিহাস তৈরি হয় অসংখ্য বর্তমানকে মালায় গেঁথে। সে ইতিহাসকে মুছতে গেলে সে জাতিও তার আপন মালা থেকে ঝরে পরবে। অন্য কারো ঠেকা নেই সে জাতিকে নিজের মালায় তুলে নেয়ার।